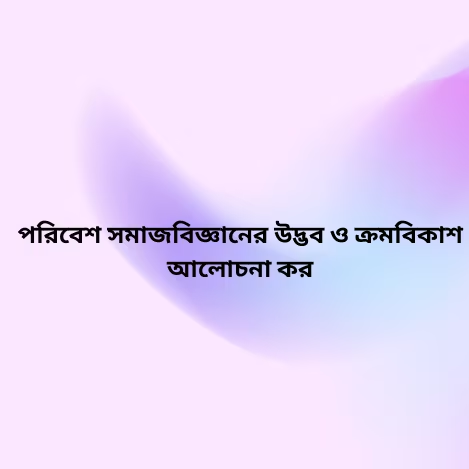
পরিবেশ সমাজ বিজ্ঞানের উদ্ভব ও বিকাশ আলোচনা কর
পরিবেশ সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ
পরিবেশ সমাজবিজ্ঞান (Environmental Sociology) হলো একটি সমাজবিজ্ঞানের শাখা যা মানুষ ও পরিবেশের মধ্যে যে সম্পর্ক তা আলোচনা করে। এর মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মানুষের পরিবেশের উপর প্রভাব এবং পরিবেশ পরিবর্তনের প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়।
পরিবেশ সমাজবিজ্ঞানের উৎপত্তি/ উদ্ভবঃ
পরিবেশ সমাজবিজ্ঞান মূলত ১৯৬০-এর দশকে পরিবেশগত আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত হয়। এই সময়টা ছিল তীব্র পরিবেশগত সংকটের সময়, যেমন দূষণ, বন ধ্বংস, এবং প্রাকৃতিক সম্পদের দ্রুত নিঃশেষ। এসময় মানুষ বুঝতে শুরু করে যে, মানব সমাজ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান, এবং এই সম্পর্ককে বোঝার জন্য আলাদা একটি সমাজবিজ্ঞানের শাখা প্রয়োজন।পরিবেশ সমাজবিজ্ঞান ১৯৭০-এর দশক থেকে বিশেষভাবে গুরুত্ব পেতে শুরু করে। মূলত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব এই শাখাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে:
- নব্য ম্যালথুসিয়ান তত্ত্ব (Neo-Malthusian Theory): এই তত্ত্বের মাধ্যমে বলা হয় যে, অতিরিক্ত জনসংখ্যা পরিবেশের উপর অতিরিক্ত চাপ তৈরি করে যা পরিবেশ সংকটের সৃষ্টি করে।
- ইকোলজিক্যাল মডার্নাইজেশন তত্ত্ব (Ecological Modernization Theory): এই তত্ত্বের মাধ্যমে বলা হয় যে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং পরিবেশগত সুরক্ষা একসাথে সম্ভব, যদি প্রযুক্তি এবং সংস্কৃতিতে যথাযথ পরিবর্তন আনা হয়।
- রাজনৈতিক পরিবেশ তত্ত্ব (Political Ecology): এই তত্ত্বের মাধ্যমে পরিবেশগত সংকটের মূলে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোকে দায়ী করা হয়। এটি ব্যাখ্যা করে কিভাবে রাজনৈতিক ও সামাজিক অসাম্য পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।
- বিপরীত আধুনিকতা তত্ত্ব (Anti-Modernity Theory): এই তত্ত্বে বলা হয় যে, আধুনিকতার কারণে প্রকৃতি থেকে দূরে সরে যাওয়া এবং পরিবেশের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতার কারণে পরিবেশের অবনতি হচ্ছে।
ক্রমবিকাশঃ
১. প্রাথমিক পর্যায় (১৯৭০-এর দশক পূর্বে)ঃ
এই পর্যায়ে, মূলধারার সমাজবিজ্ঞান পরিবেশের বিষয়টিকে সেভাবে গুরুত্ব দেয়নি। প্রাথমিক পর্যায়ে মনে করা হতো, সমাজের মূল বিষয়বস্তু হল মানুষ এবং তার সামাজিক কাঠামো, আর প্রকৃতি ছিল সমাজের বাইরের কিছু। তবে ১৮ শতকের ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভোলিউশনের পর থেকে ক্রমশ মানবজাতির সঙ্গে পরিবেশের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে ভাবনা শুরু হয়।
২. পরিবেশ আন্দোলন এবং পরিবেশ সমাজবিজ্ঞানের আবির্ভাব (১৯৭০-এর দশক)
১৯৭০-এর দশকে পরিবেশ নিয়ে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা বৃদ্ধি পায়। সে সময়ের পরিবেশগত সংকট যেমন দূষণ, বনভূমি ধ্বংস, জলবায়ু পরিবর্তন ইত্যাদি ইস্যু সমাজবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ সময়ই পরিবেশ সমাজবিজ্ঞানের মূল ভিত্তি তৈরি হয়, এবং সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী এবং গোষ্ঠীর সাথে পরিবেশের পারস্পরিক প্রভাব নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। মূলত, আমেরিকান সমাজবিজ্ঞানী উইলিয়াম ক্যাটন ও রাইলি ডানল্যাপ ১৯৭৮ সালে তাদের বিখ্যাত নিবন্ধে “Ecological Paradigm” ধারণা দেন। এই ধারণা বলছিল যে, মানুষ প্রকৃতির বাইরে নয়, বরং প্রকৃতির অংশ।
৩. আধুনিক যুগ এবং ক্রমবিকাশ (১৯৮০-এর দশক থেকে বর্তমান)
১৯৮০-এর দশক থেকে বর্তমান পর্যন্ত পরিবেশ সমাজবিজ্ঞান আরো বিস্তৃত হয়। আধুনিক পরিবেশ সমাজবিজ্ঞান বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন, টেকসই উন্নয়ন, পরিবেশ ন্যায়বিচার, এবং পরিবেশগত ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে। এছাড়া, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ কীভাবে পরিবেশের ওপর প্রভাব ফেলে এবং পরিবেশ পরিবর্তনের কারণে কীভাবে সামাজিক পরিবর্তন ঘটে—এসব বিষয় নিয়ে গবেষণা শুরু হয়।
উপসংহার:
পরিবেশ সমাজবিজ্ঞান একটি নতুন ও দ্রুত বিকাশমান শাখা, যা সমাজের কাঠামো, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, এবং মানুষের কার্যক্রমের কারণে পরিবেশের উপর যে প্রভাব পড়ছে, তা বিশ্লেষণ করে। এটি মানবসমাজ এবং প্রকৃতির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককে নতুন আঙ্গিকে বোঝার চেষ্টা করে, যা বর্তমান বিশ্বে পরিবেশগত নীতি ও সমস্যাগুলো সমাধানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
