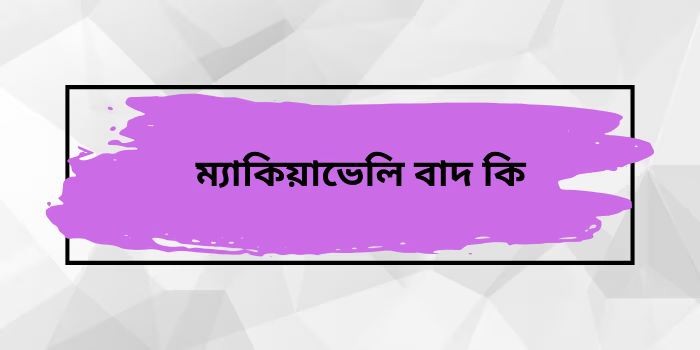সমালোচনাসহ প্লেটোর ন্যায়বিচার তত্ত্বটি আলোচনা কর।
প্লেটোর ন্যায়বিচার তত্ত্ব প্রাচীন গ্রিক দর্শনের এক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ, যা…
প্লেটোর ন্যায়বিচার তত্ত্ব প্রাচীন গ্রিক দর্শনের এক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ, যা তার বিখ্যাত গ্রন্থ ‘দ্য রিপাবলিক’-এর মূল আলোচ্য বিষয়। এটি কেবল আইনি ধারণা নয়, বরং ব্যক্তি ও সমাজের আত্মিক শৃঙ্খলা এবং সামঞ্জস্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্লেটোর এই তত্ত্ব একটি আদর্শ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য নৈতিক ভিত্তি প্রদান করে। তিনি বিশ্বাস করতেন, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী যখন নিজ নিজ কর্তব্য পালনে ব্রতী হয় এবং অন্যের কাজে হস্তক্ষেপ করে না, তখনই প্লেটোর ন্যায়বিচার তত্ত্ব (Plato’s Theory of Justice) প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি মানব আত্মার তিনটি উপাদানের (প্রজ্ঞা, সাহস ও প্রবৃত্তি) মধ্যে ভারসাম্য এবং সমাজে তিনটি শ্রেণীর (দার্শনিক শাসক, সৈনিক ও উৎপাদক) কর্মভিত্তিক বিশেষীকরণের ওপর জোর দেয়।
প্লেটোর ন্যায়বিচার তত্ত্ব
গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর মতে, ন্যায়বিচার (Justice) কোনো বাহ্যিক বিষয় বা কৃত্রিম চুক্তি নয়; এটি হলো মানব আত্মার একটি স্বাভাবিক গুণ এবং সমাজের একটি স্বাভাবিক নীতি। তাঁর প্লেটোর ন্যায়বিচার তত্ত্ব মূলত দুটি স্তরে বিচার করা যায়: ব্যক্তিগত ন্যায় এবং রাষ্ট্রীয় ন্যায়।
১. ব্যক্তিগত ন্যায় (Individual Justice)
ব্যক্তির আত্মার তিনটি মৌলিক উপাদান রয়েছে:
প্রজ্ঞা (Reason/Wisdom): এটি হলো জ্ঞানের প্রতি আকাঙ্ক্ষা এবং যুক্তি দিয়ে চিন্তা করার ক্ষমতা। প্লেটো মনে করেন, আত্মার এই অংশটি শাসন করা উচিত।
সাহস (Spirit/Courage): এটি হলো উদ্দীপনা, ক্রোধ এবং বিপদ মোকাবেলার ক্ষমতা। এটি প্রজ্ঞার নির্দেশ মেনে চলে।
প্রবৃত্তি (Appetite): এটি হলো ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যৌনতা ইত্যাদি দৈহিক চাহিদা। এটি অবশ্যই প্রজ্ঞা ও সাহসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে হবে।
যখন প্রজ্ঞা, সাহস এবং প্রবৃত্তি নিজ নিজ সীমা মেনে চলে এবং প্রজ্ঞার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তখনই ব্যক্তির জীবনে প্লেটোর ন্যায়বিচার তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।
২. রাষ্ট্রীয় ন্যায় (Social Justice)
প্লেটো রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির আত্মার একটি সাদৃশ্য (Analogy) টেনেছেন। ব্যক্তির আত্মার তিনটি উপাদানের ভিত্তিতে তিনি সমাজে তিনটি শ্রেণী চিহ্নিত করেছেন:
দার্শনিক শাসক শ্রেণী (Philosopher Rulers): এদের মধ্যে প্রজ্ঞা গুণটি প্রধান, এবং এরাই রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে।
সৈনিক বা সহায়ক শ্রেণী (Auxiliaries/Soldiers): এদের মধ্যে সাহস গুণটি প্রধান, এবং এরা রাষ্ট্রকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করবে।
উৎপাদক শ্রেণী (Producers): এদের মধ্যে প্রবৃত্তি গুণটি প্রধান, এবং এরা সমাজের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপাদন করবে।
প্লেটোর মতে, সমাজের প্রতিটি শ্রেণী যখন তাদের নির্দিষ্ট কাজগুলো (অর্থাৎ, কর্মবিশেষীকরণ) নিষ্ঠার সাথে পালন করবে এবং কোনো শ্রেণী অন্য কোনো শ্রেণীর কাজে হস্তক্ষেপ করবে না, তখনই সমাজে প্লেটোর ন্যায়বিচার তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। এই কর্মবিভাজনের মাধ্যমেই সমাজে সংহতি ও ঐক্য আসে।
প্লেটোর ন্যায়বিচার তত্ত্বের মূল বৈশিষ্ট্য
- অভ্যন্তরীণ গুণ: প্লেটোর ন্যায়বিচার তত্ত্ব কোনো আইনি বা বাহ্যিক ব্যবস্থা নয়, বরং এটি ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা (Inner Harmony)।
- কর্মবিশেষীকরণ (Functional Specialisation): সমাজের প্রতিটি শ্রেণী নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করবে এবং অন্যের কাজে হস্তক্ষেপ করবে না। এটি প্লেটোর ন্যায়বিচার তত্ত্ব-এর মূল ভিত্তি।
- অহস্তক্ষেপ নীতি (Principle of Non-interference): এক শ্রেণীর কাজে অন্য শ্রেণীর হস্তক্ষেপ না করার নীতিই প্লেটোর ন্যায়বিচার তত্ত্ব।
- নৈতিক ধারণা (Ethical Concept): এটি একটি নৈতিক ধারণা, আইনি বাধ্যবাধকতা নয়। এটি মানুষকে তাদের কর্তব্য পালনে উৎসাহিত করে।
- শ্রেণীগত সামঞ্জস্য: তত্ত্বটি সমাজে দার্শনিক, সৈনিক ও উৎপাদক এই তিনটি শ্রেণীর মধ্যে একটি সুষ্ঠু সামঞ্জস্য (Harmony) প্রতিষ্ঠা করে।
- আদর্শ রাষ্ট্রের ভিত্তি: প্লেটোর কল্পনা করা আদর্শ রাষ্ট্রের মূল ভিত্তিই হলো এই ন্যায়বিচার তত্ত্ব।
- শিক্ষার ভূমিকা: দার্শনিক শাসক এবং সৈনিক শ্রেণীকে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।
- দায়িত্বের ওপর জোর: তত্ত্বটি অধিকারের চেয়েও ব্যক্তির কর্তব্য ও দায়িত্বের ওপর অধিক জোর দেয়।
প্লেটোর ন্যায়বিচার তত্ত্বের সমালোচনা
প্লেটোর এই তত্ত্বটি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচিত হয়েছে:
- ব্যক্তির অধিকারের অবহেলা: সমালোচকরা বলেন, প্লেটোর ন্যায়বিচার তত্ত্ব কেবল কর্তব্যের ওপর জোর দেয়, কিন্তু ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতাকে উপেক্ষা করে।
- শ্রেণী বিভাজন: কঠোর শ্রেণী বিভাজন সমাজকে স্থিতিশীল করার বদলে সামাজিক গতিশীলতা (Social Mobility) নষ্ট করে এবং শ্রেণী সংঘাতের জন্ম দিতে পারে।
- সর্বাত্মকবাদী প্রবণতা (Totalitarian Tendencies): দার্শনিক শাসকের হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতা (Unchecked Power) কেন্দ্রীভূত হওয়ার কারণে কার্ল পপারসহ অনেক আধুনিক সমালোচক প্লেটোর তত্ত্বকে সর্বাত্মকবাদী বলে অভিহিত করেছেন।
- অবাস্তব ধারণা: দার্শনিক শাসকের ধারণাটি অবাস্তব ও কল্পনাপ্রসূত, কারণ বাস্তবে নিখুঁত এবং দুর্নীতিমুক্ত শাসক খুঁজে পাওয়া কঠিন।
- আইনের প্রতি উদাসীনতা: প্লেটো তার ন্যায়বিচার তত্ত্বে আইনি শাসন (Rule of Law) বা সাংবিধানিক সুরক্ষার ওপর গুরুত্ব দেননি, যা আধুনিক রাষ্ট্রে অপরিহার্য।
- ব্যক্তির সামগ্রিক বিকাশ রোধ: কর্মবিশেষীকরণ ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট গণ্ডিতে আবদ্ধ করে, যা তার সমগ্র ব্যক্তিত্বের বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে।
উপসংহার
প্লেটোর প্লেটোর ন্যায়বিচার তত্ত্ব ব্যক্তি ও সমাজের জন্য নৈতিক শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্যের এক মহৎ ধারণা পেশ করে। সমালোচিত হওয়া সত্ত্বেও, ন্যায়কে একটি নৈতিক সদ্গুণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে এই তত্ত্ব পশ্চিমা রাজনৈতিক চিন্তাধারার ইতিহাসে এক চিরন্তন প্রভাব বিস্তার করেছে। প্লেটোর এই প্লেটোর ন্যায়বিচার তত্ত্ব মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণাবলীকে কাজে লাগিয়ে একটি আদর্শ, ঐক্যবদ্ধ ও স্থিতিশীল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিয়েছিল, যা আজও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে।