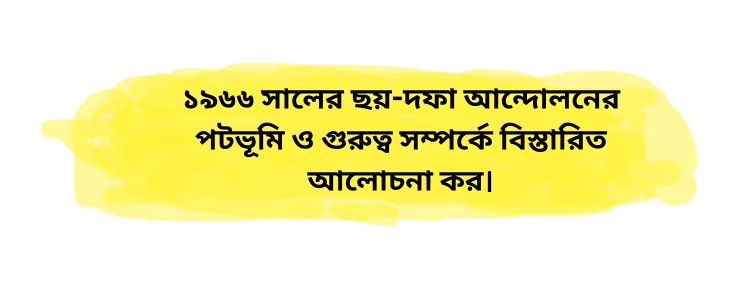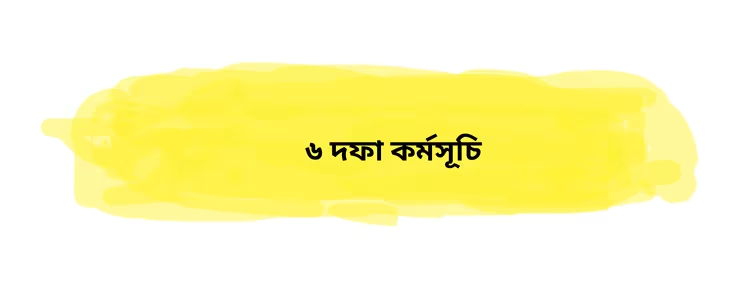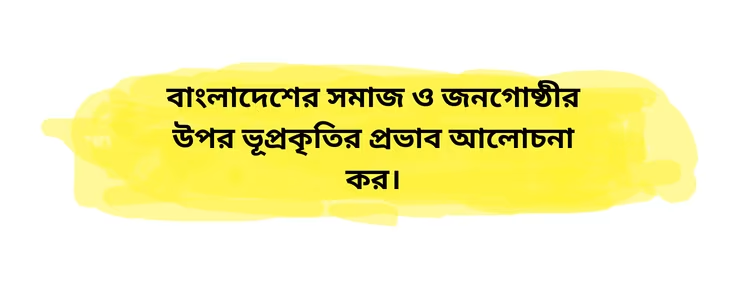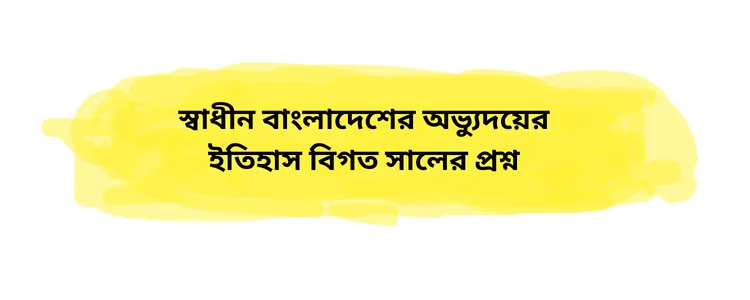ঔপনিবেশিক শাসন আমলে বাংলায় সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও বিকাশ
ঔপনিবেশিক শাসন আমলে বাংলায় সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও বিকাশ সাম্প্রদায়িকতা (Communalism)…
ঔপনিবেশিক শাসন আমলে বাংলায় সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও বিকাশ
সাম্প্রদায়িকতা (Communalism) একটি এমন রাজনৈতিক মতাদর্শ, যেখানে একটি ধর্মীয় গোষ্ঠীর স্বার্থকে অন্য ধর্মীয় গোষ্ঠীর স্বার্থের থেকে আলাদা, এমনকি প্রতিপক্ষ হিসেবে গণ্য করা হয়। এটি ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে গোষ্ঠীগত আনুগত্যকে জাতীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান দেয়। বাংলায়, মুঘল শাসনের পতনের পর এবং ব্রিটিশ শাসনের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বাংলায় সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে, যা শেষ পর্যন্ত ১৯৪৭ সালের দেশভাগের মাধ্যমে বাংলার বিভাজনকে অনিবার্য করে তোলে।
বাংলায় সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও বিকাশ
১. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩)
১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস কর্তৃক প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলায় সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও বিকাশ এর একটি প্রাথমিক ও প্রধান কারণ। এই ব্যবস্থার ফলে এক নতুন জমিদার শ্রেণির সৃষ্টি হয়, যাদের অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু। অন্যদিকে, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম কৃষক সম্প্রদায় তাদের জমিতে অধিকার হারিয়ে দরিদ্র প্রজা ও ভূমিহীন খেতমজুরে পরিণত হয়। এই অর্থনৈতিক বৈষম্য, যেখানে জমিদার/মহাজন ছিলেন হিন্দু এবং প্রজা/খাতক ছিলেন মুসলমান, শোষক ও শোষিতকে ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে দাঁড় করায়, যা বাংলায় সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও বিকাশ কে ত্বরান্বিত করে।
২. ব্রিটিশ শিক্ষানীতির প্রভাবঃ
ব্রিটিশ প্রবর্তিত পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণে হিন্দু সম্প্রদায় প্রথমদিকে এগিয়ে যায়। এর ফলে সরকারি চাকরি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা লাভে তারা এগিয়ে থাকে। মুসলমানরা তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে ছিল। উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি মুসলমানরা যখন আধুনিক শিক্ষায় আগ্রহী হয়ে ওঠে, ততদিনে হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণি প্রশাসনে ও পেশাগত ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। এই শিক্ষাগত ও পেশাগত বৈষম্য থেকেই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়, যা বাংলায় সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও বিকাশ এর রাজনৈতিক ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।
৩. ‘বিভক্ত করো ও শাসন করো’ নীতি (Divide and Rule Policy)
ব্রিটিশ সরকার তাদের শাসনকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য সচেতনভাবে ‘বিভক্ত করো ও শাসন করো’ নীতি প্রয়োগ করেছিল। তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সম্প্রদায়কে একে অপরের বিরুদ্ধে উসকে দেয় এবং তাদের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করে। বঙ্গভঙ্গের (১৯০৫) মতো ঘটনা এই নীতির চরম বহিঃপ্রকাশ, যা বাংলায় সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও বিকাশ কে দ্রুতগামী করে তোলে।
৪. ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ পরবর্তী ধর্মীয় মেরুকরণ
১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর ব্রিটিশরা প্রাথমিকভাবে মুসলিমদেরকেই প্রধান প্রতিপক্ষ মনে করত। পরবর্তীতে যখন ভারতীয় জাতীয়তাবাদ শক্তিশালী হতে থাকে, তখন ব্রিটিশরা রাজনৈতিক স্বার্থে হিন্দু-মুসলিম বিভেদকে কাজে লাগাতে শুরু করে। ধর্মীয় পরিচয়কে কেন্দ্র করে জনগণের মধ্যে মেরুকরণ সৃষ্টি হয়, যা বাংলায় সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও বিকাশ এর ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ মোড়।
৫. ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন ও পুনরুত্থানবাদ (Religious Revivalism)
উনবিংশ শতকে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই সংস্কার আন্দোলন দেখা গিয়েছিল। তবে এই আন্দোলনগুলি অনেক সময়ই রক্ষণশীল ও পুনরুত্থানবাদী (Revivalist) চরিত্র গ্রহণ করে, যা অন্য সম্প্রদায়ের ধর্মীয় ও সামাজিক রীতিনীতিকে আক্রমণ করত। যেমন, হিন্দু সমাজে ‘আর্য সমাজ আন্দোলন’ বা মুসলিম সমাজে ‘ফরায়েজী আন্দোলন’-এর মতো কিছু ধারা অন্যদের থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে এবং বাংলায় সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও বিকাশ কে সাংস্কৃতিক রূপ দেয়।
৬. বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫)ঃ
লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ (Partition of Bengal) ছিল বাংলায় সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও বিকাশ এর ইতিহাসে এক জলন্ত উদাহরণ। বাংলাকে দুটি প্রদেশে বিভক্ত করার সরকারি উদ্দেশ্য প্রশাসনিক হলেও, এর পিছনে ছিল পূর্ববঙ্গের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল এবং পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনে হিন্দু ধর্মীয় প্রতীক ও আচার-ব্যবহারের অধিক ব্যবহার মুসলমান সম্প্রদায়কে আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, যা বাংলায় সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও বিকাশ কে আরও দৃঢ় করে।
৭. পৃথক নির্বাচন প্রথা (Minto-Morley Reforms, 1909)
১৯০৯ সালের মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইনে মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন প্রথা চালু করা হয়। এর ফলে মুসলিম ভোটাররা কেবল মুসলিম প্রার্থীকেই ভোট দিতে পারত। এই ব্যবস্থা রাজনৈতিকভাবে হিন্দু ও মুসলিমদের স্বার্থকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেয় এবং ধর্মীয় পরিচয়কে রাজনীতির মূল ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। এই বিভেদ নীতি বাংলায় সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও বিকাশ এর প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি তৈরি করে।
৮. সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলগুলোর উত্থান
বিশ শতকের প্রথম দিকে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ (All India Muslim League, ১৯০৬) এবং হিন্দু মহাসভার (Hindu Mahasabha) মতো সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলগুলোর উত্থান বাংলায় সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও বিকাশ কে ত্বরান্বিত করে। এই দলগুলো তাদের নিজ নিজ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের স্বার্থকে জাতীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে স্থান দিতে শুরু করে এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য ধর্মীয় আবেগকে ব্যবহার করে।
৯. সাংস্কৃতিক ও ভাষাভিত্তিক বিভেদ
বাংলা ভাষার উপর আরবি-ফারসি বনাম সংস্কৃত ভাষার প্রভাবের প্রশ্ন এবং সাংস্কৃতিক প্রতীক ও অনুষ্ঠানের ভিন্নতাও বাংলায় সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও বিকাশ এ ভূমিকা রাখে। সাহিত্য ও শিক্ষাব্যবস্থায় দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সাংস্কৃতিক দূরত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় তারা নিজেদেরকে দুটি ভিন্ন জাতি হিসেবে ভাবতে শুরু করে।
১০. ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন ও জোট গঠনের ব্যর্থতা
১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনের পর বাংলার প্রাদেশিক আইনসভায় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে জোট সরকার গঠনে ব্যর্থতা বাংলায় সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও বিকাশ কে আরও গভীর করে। এই রাজনৈতিক অচলাবস্থা উভয় দলের নেতাদেরকে চরমপন্থার দিকে ঠেলে দেয় এবং দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তি মজবুত হয়।
১১. লাহোর প্রস্তাব (১৯৪০) ও পাকিস্তান আন্দোলনঃ
১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে পৃথক রাষ্ট্র গঠনের দাবি (যা পরবর্তীতে পাকিস্তান নামে পরিচিতি লাভ করে) বাংলায় সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও বিকাশ এর চূড়ান্ত পর্যায়কে চিহ্নিত করে। এর ফলে ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে ভারত বিভাজন প্রায় অনিবার্য হয়ে ওঠে। মুসলিম লীগ এই ধারণাকে বাংলার মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করে।
১২. ১৯৪৬ সালের দাঙ্গা ও দেশভাগের অনিবার্যতা
১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট মুসলিম লীগ কর্তৃক ঘোষিত ‘প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস’ কে কেন্দ্র করে কলকাতা, নোয়াখালী এবং অন্যান্য স্থানে যে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (Great Calcutta Killings) সংঘটিত হয়েছিল, তা বাংলায় সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও বিকাশ এর চরম পরিণতি। এই রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও ভীতি এমন পর্যায়ে নিয়ে যায় যে, দেশভাগই একমাত্র সমাধান বলে প্রতীয়মান হয়।
উপসংহার:
ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন আমলে বাংলায় সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব ও বিকাশ ছিল এক বহুমাত্রিক প্রক্রিয়া। এটি কেবল ধর্মীয় বা রাজনৈতিক বিরোধ ছিল না, বরং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থেকে উদ্ভূত আর্থ-সামাজিক বৈষম্য, শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চাৎপদতা, এবং ব্রিটিশদের কূটনীতির এক জটিল জাল ছিল। যদিও বাংলার ঐতিহ্যগত সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সম্প্রীতির একটি দীর্ঘ ইতিহাস ছিল, তবে ঔপনিবেশিক শক্তির স্বার্থপর নীতি এবং উভয় সম্প্রদায়ের নেতাদের কিছু সংকীর্ণ সিদ্ধান্ত সমাজে বিভেদের প্রাচীর গড়ে তোলে। এর চরম পরিণতি হলো ১৯৪৭ সালে বাংলা ও ভারতের বিভাজন। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এই আলোচনা আমাদের শিক্ষা দেয় যে, আর্থ-সামাজিক ন্যায্যতা এবং রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব কীভাবে একটি সমাজের দীর্ঘদিনের সম্প্রীতিকে নষ্ট করে দিতে পারে। আজও, বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে সেই বিভাজনের ক্ষত ও উত্তরাধিকার বয়ে চলেছে, যা থেকে মুক্তির জন্য অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও সমতার ভিত্তিতে সমাজের পুনর্গঠন জরুরি।।