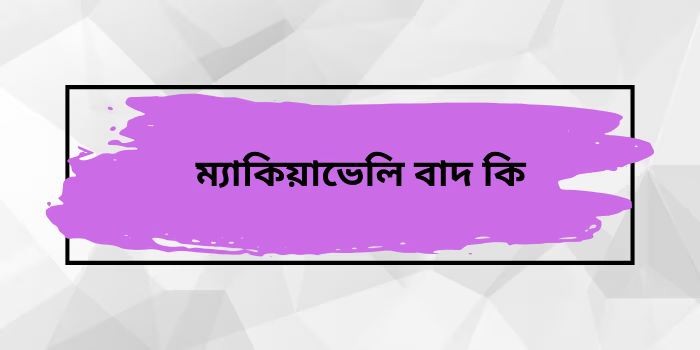জন অস্টিনের সার্বভৌম তত্ত্বটি আলোচনা কর।
জন অস্টিনের সার্বভৌম তত্ত্বটি আলোচনা কর। ভূমিকা: উনবিংশ শতকের ব্রিটিশ…
জন অস্টিনের সার্বভৌম তত্ত্বটি আলোচনা কর।
ভূমিকা:
উনবিংশ শতকের ব্রিটিশ আইনবিদ জন অস্টিন প্রদত্ত সার্বভৌম তত্ত্ব (Monistic Theory of সার্বভৌম তত্ত্ব) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক। এটি আইনানুগ সার্বভৌমত্বের একত্ববাদী মতবাদ হিসেবে পরিচিত, যা হবস ও বেস্থামের ধারণার উপর ভিত্তি করে বিকশিত হয়েছে। অস্টিন আইনকে নৈতিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি ‘আদেশ, সার্বভৌম এবং অনুমোদন’ নির্ভর কাঠামোয় স্থাপন করেছেন। এই তত্ত্বের মূল কথা হল, সমাজে একটি নির্দিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ থাকে, যার আদেশই আইন এবং যার আনুগত্য জনগণ অভ্যাসবশত করে থাকে। (৬৬ শব্দ)
জন অস্টিনের সার্বভৌম তত্ত্বের মূল আলোচনা (Main Points)
জন অস্টিনের সার্বভৌম তত্ত্ব বিশ্লেষণী বা একত্ববাদী মতবাদ নামে পরিচিত। এই তত্ত্বের মূল লক্ষ্য হলো আইন ও সার্বভৌম তত্ত্ব-এর প্রকৃতিকে সুস্পষ্ট ও যৌক্তিক কাঠামোর মধ্যে তুলে ধরা। তার মতে, আইন হলো সার্বভৌম তত্ত্ব-এর আদেশ, যা শাস্তি বা অনুমোদনের ভয় দ্বারা সমর্থিত।
১. নির্দিষ্ট মানব ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ (Determinate Human Superior): অস্টিনের মতে, সার্বভৌম তত্ত্ব ক্ষমতা অবশ্যই একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকবে। এই ‘নির্দিষ্ট মানব ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ’ সমাজের বাকি অংশ থেকে আলাদা এবং তারাই আইন প্রণয়ন করে।
২. অভ্যাসবশত আনুগত্য (Habitual Obedience): সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ অভ্যাসবশত এবং নিয়মিতভাবে সার্বভৌম তত্ত্ব-এর আদেশ মেনে চলবে। এই আনুগত্য স্বতঃস্ফূর্ত বা বাধ্যতামুলক উভয়ই হতে পারে, কিন্তু এটি সমাজের একটি নিয়মিত অভ্যাস হতে হবে।
৩. ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অন্যের প্রতি অনানুগত্য: যে কর্তৃপক্ষ সার্বভৌম তত্ত্ব-এর অধিকারী, সে নিজে অন্য কোনো ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ বা নিয়ন্ত্রণের অধীন হবে না। সার্বভৌম তত্ত্ব নিজের ক্ষমতার ক্ষেত্রে স্বাধীন ও চরম।
৪. আইনের উৎস হিসেবে আদেশ (Law as a Command): অস্টিনের মতে, আইন হল সার্বভৌম তত্ত্ব-এর আদেশ। এই আদেশ নির্দেশমূলক এবং বাধ্যতামূলক। আইনের এই ধারণা নৈতিকতা বা প্রথাগত রীতিনীতি থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন।
৫. অনুমোদন বা শাস্তি (Sanction): সার্বভৌম তত্ত্ব-এর আদেশ অমান্য করলে শাস্তির ব্যবস্থা থাকবে। অস্টিনের তত্ত্বে শাস্তি বা অনুমোদনের ভয়ই সার্বভৌম তত্ত্ব-এর প্রতি আনুগত্যের অন্যতম কারণ।
৬. সার্বভৌম ক্ষমতার অবিভাজ্যতা (Indivisibility): সার্বভৌম তত্ত্ব ক্ষমতা অবিভাজ্য এবং অসীম। এটি কোনোভাবেই বিভক্ত বা সীমিত করা যায় না। একাধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করে দিলে সার্বভৌম তত্ত্ব-এর ধারণাই বিঘ্নিত হবে।
৭. অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সার্বভৌমত্ব (Internal and External Sovereignty): অস্টিনের সার্বভৌম তত্ত্ব অভ্যন্তরীণভাবে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা নির্দেশ করে এবং বাহ্যিকভাবে রাষ্ট্রকে অন্যান্য রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ থেকে স্বাধীনতা প্রদান করে।
৮. আইনি সার্বভৌমত্ব (Legal Sovereignty): এই তত্ত্ব সার্বভৌম তত্ত্ব-এর আইনি বা আইনগত দিকের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়। আইন প্রণয়নের চূড়ান্ত ক্ষমতা যেখানে থাকে, সেটাই অস্টিনের কাছে সার্বভৌম তত্ত্ব।
৯. সার্বভৌম তত্ত্ব-এর অবাধ ক্ষমতা (Absolute Power): সার্বভৌম তত্ত্ব-এর ক্ষমতা কোনো আইন দ্বারা সীমিত নয়। অস্টিন সার্বভৌম তত্ত্ব-এর অবাধ ক্ষমতাকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ও চূড়ান্ত ক্ষমতা হিসেবে তুলে ধরেছেন।
১০. আইন ও নৈতিকতার বিচ্ছেদ (Separation of Law and Morality): অস্টিন ইতিবাচক আইনের উপর জোর দেন, যা নৈতিকতা, ধর্ম বা প্রথাগত রীতিনীতি থেকে আলাদা। তার কাছে আইন ‘যেমন আছে’, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ, ‘যেমন হওয়া উচিত’ তা নয়।
সমালোচনা ও গুরুত্ব:
জন অস্টিনের সার্বভৌম তত্ত্ব তার স্পষ্ট ও বিশ্লেষণধর্মী কাঠামোর জন্য আইনি চিন্তাধারায় অত্যন্ত প্রভাবশালী। তবে এই তত্ত্ব সার্বভৌম তত্ত্ব-এর চরম ও অবিভাজ্য প্রকৃতির উপর জোর দেওয়ায় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এবং আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রে সমালোচিত হয়েছে। এটি জনমত, প্রথা বা নৈতিকতার মতো বিষয়গুলিকে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে অগ্রাহ্য করেছে, যা আধুনিক রাজনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে সম্পূর্ণ মেলে না। তবুও, এই তত্ত্ব আইন ও সার্বভৌম তত্ত্ব-এর ধারণাকে সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে এবং আইনি বিশ্লেষণবাদের ভিত্তি স্থাপন করেছে।